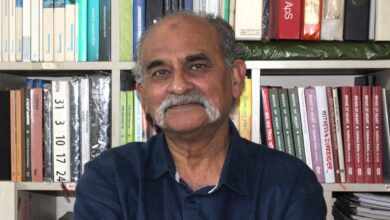কাজী আরেফের মতো মুক্তিযোদ্ধার মূল্যায়ন হয়নি আজও!

ওরা আমাকে মিছিল করার একটা ফটো দেখায়। তখন অকপটেই স্বীকার করি, ‘হ্যাঁ, আমি মিছিল করেছি, আমি ছাত্রলীগ করি।’
“ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন। ১৪ অগাস্ট স্কুল থেকে নিয়ে যাবে স্টেডিয়ামে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান হবে। সকালে রেডি হয়ে বের হচ্ছি। পাশের রুমে বাবা তার চেম্বারে বসা।
দেখে বললেন, ‘কোথায় যাচ্ছ?’ বললাম, ‘স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা দিবস আজ।’
তিনি কেন যেন চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর বেরিয়ে এসে বললেন, ‘ওখানে তুমি যাবে না। এটা আমাদের স্বাধীনতা দিবস নয়।’ শুনে খুব মন খারাপ হলো। বন্ধুরা যাবে, আমি যাব না। কান্নাও করেছিলাম।
পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস কেন আমাদের স্বাধীনতা দিবস নয়? এই প্রশ্ন করার সাহস তখন হয়নি। কিন্তু এখন বুঝি ওইসময় বাবা আমার মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি বীজ বপন করে দিয়েছিলেন।”
বাবার স্মৃতিচারণ এভাবেই একটি ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রওশন জাহান সাথী। এক সকালে তার বাড়িতে বসেই কথা হয় একাত্তর ও স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে।
তার মায়ের নাম বেগম নুরুন নাহার আর বাবা অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন। বাড়ি ভারতের চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁও মহাকুমার সবাইপুর গ্রামে। দেশ ভাগের পর বনগাঁও থেকে তারা স্থায়ীভাবে চলে আসেন যশোরে।
সাথীর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি বনগাঁওয়ে, সবাইপুর প্রাইমারি স্কুলে। পরে যশোরে এসে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হন, যশোর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৬৬ সালে। অতঃপর ভর্তি হন যশোর মহিলা কলেজে। ১৯৬৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে একই কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেন তিনি।
বাবা অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন ছয় দফা আন্দোলনের সময় যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন, সভাপতি ছিলেন নূর বক্স। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে যশোর থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) নির্বাচিত হন তিনি।
পরিবারে রাজনৈতিক আবহই রওনক জাহান সাথীকে রাজনীতির প্রতি উৎসাহী করে তোলে। ১৯৬৮ সালে যশোর সদর মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৬৯ সালে যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হন সাথী।

সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশে ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের ভেতর একটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। সেই নিউক্লিয়াসে ছিলেন তিনজন ব্যক্তি— সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ। তারা চেয়েছিলেন আন্দোলনটিকে স্বাধীনতামুখী করতে।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু যখন জেলে তখন ওই আন্দোলনটাকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়। নিউক্লিয়াসের গোপন সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হয় ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ’। ১৯৭০ সালে ওই গোপন সংগঠনের যশোর ফোরামের সদস্য করা হয় সাথীকে। কেন্দ্র থেকে ওই কমিটি করতে এসেছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ।
সত্তরের নির্বাচনে যশোর থেকে এমপিএ নির্বাচিত হন তার বাবা মোশাররফ হোসেন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কারা ছিলেন?
সাথী বলেন, “মুসলিম লীগের শামসুল হুদা, অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান, মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ ছিলেন বিপক্ষে। এরাই পরবর্তীতে যশোরে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠন করেন। এছাড়া একটি গোপন বামপন্থী সংগঠনও তখন নির্বাচনকে কটাক্ষ করে যশোরে দেয়াল লেখন করে। লেখা ছিল এমন, ‘শুয়োরের বাচ্চা জনগণ, করবি তোরা নির্বাচন, আমরা গেলাম সুন্দরবন।’ এটা দেখে খুব খারাপ লেগেছিল।”
তখন মানুষ ভাবত, শেখ মুজিব মানুষটা আমাদেরই। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় ইমেজ। আরেকটি হলো সাংগঠনিক তৎপরতা। এই দুয়ের কারণেই সত্তরের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ।
কিন্তু তবুও ক্ষমতা না দিতে ষড়যন্ত্র শুরু করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। ১ মার্চ তারা পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু তখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।
যশোরে তখন আপনারা কী করলেন?
তার ভাষায়, “৩ মার্চ ১৯৭১। মাইকট্টিতে মিছিলে গুলি চলে। গুলিতে নিহত হয় এক গৃহবধু, নাম চারুবালা কর। আর্মিদের ছোড়া গুলিটি তার মাথায় বিদ্ধ হয়। ওইদিন তার শবদেহ নিয়ে বিশাল মিছিল বের করি আমরা।
বিশ তারিখের পর মিছিল সার্কিট হাউজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওইসময় আর্মিরা গুলি চালালে ধরেরবাড়ি নামক জায়গায় লালু নামের এক কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়। তবুও যশোরে প্রতিবাদের মিছিল বন্ধ করা যায়নি।”
২৫ মার্চ ১৯৭১। রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি সেনারা।
যশোরে কী ঘটল?
সাথীর ভাষায়, “ওইদিন সকালবেলা যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি কর্নেল তোফায়েল সকল এমপিএ ও এমএনএদের নিয়ে বৈঠক করেন। তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তখনও লাগানো ছিল। মিটিংয়ে সকলকে শান্তি বজায় রাখার কথা বলেন কর্নেল।
বৈঠক শেষে বের হয়ে এমপিএ ও এমএনএরা দেখলেন তাদের গাড়িতে লাগানো বাংলাদেশের পতাকা নেই। পাকিস্তানি আর্মিরা সেটা খুলে নিয়েছে। বাবার (মোশাররফ হোসেন) নেতৃত্বে তখনই প্রতিবাদ করেন সবাই।
বাবা বললেন, ‘পতাকা যে নিয়েছে তাকে নিয়ে আসতে বলেন’।
কর্নেল তোফায়েল বেশ বিব্রত হন, ভেতরে ভেতরে রাগান্বিতও। তার নির্দেশে বাংলাদেশের পতাকাগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যাওয়ার সময় সন্ধ্যায় সবাইকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানান এবং এমপিএ ও এমএনএরা যেন উপস্থিত থাকেন বিশেষভাবে তা উল্লেখ করেন কর্নেল তোফায়েল।
ফিরে এসে আওয়ামী লীগের সবাই মশিউর রহমানের বাসায় বসলেন। খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে এটা টের পান সবাই। বাবা বললেন, ‘এ ডিনার হলো ফাঁদ। সেখানে আমাদের যাওয়া উচিত হবে না। কেউ যাবে না ডিনারে।’
সন্ধ্যায় নেতারা জড়ো হন আমাদের বাড়িতে। বাবা ছিলেন স্বাধীনতাপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা। সবাইকে তিনি বলেন, কেউ যেন শহরে না থাকে। আগেই কিছু অস্ত্র জোগাড় করা ছিল।
যশোরে নামকরা জুতোর দোকান ছিল পাদুকা ভবন। সেখান থেকে আনা হয় অনেক কেডস। ছেলেরা স্যান্ডেল খুলে কেডস পরে শহরের বাইরে চলে যায়, একেবারেই যুদ্ধের প্রস্তুতি। তাদের সঙ্গে বাবাও চলে গেলেন। অতঃপর রাত ১০টার দিকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মি মুভ করে।”
আপনারা কি তখন বাড়িতেই ছিলেন?
“না। বসন্তকুমার রোডে বড় চাচার বাড়িতে চলে যাই। ২৬ মার্চ সকালে চাচাত ভাই মাসুকুর রহমান তোজো থানার পাশে তার এক মামার বাড়িতে নিয়ে যান।

ওখানেই দেখা করতে আসেন আব্দুল মোনায়েম চাচা। আমাকে লেখা বাবার একটা চিরকুট পৌঁছে দেন তিনি। লেখা ছিল এমন, ‘সাথী, আমরা যুদ্ধে চলে গেলাম। তুমি সবাইকে নিয়ে ঠিকমতো থেক। আশা করি দেখা হবে। ইতি বাবু।’ চিরকুটটা দেখেই ছিড়ে ফেলি।
বেলা তখন তিনটা। হঠাৎ পাকিস্তানি আর্মিরা বাড়িটা ঘিরে ফেলে। কর্নেল তোফায়েল নিজে এসেছিলেন বাবাকে (মোশাররফ হোসেন) খুঁজতে।
সব মেয়েরা বাড়ির দোতলায়। বন্দুক তাক করে সেখানে উঠে এলো এক আর্মি।
বলে, ‘মোশাররফ ছাবকা আওরাত কোন হে?’ সবাই ভয়ে চুপ মেরে আছে। মহিলারাও কাঁপছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।
বলে, ‘ইধার আও।’ নিচে কর্নেল তোফায়েলের কাছে নিয়ে গেল। নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তিনি।
বললেন, ‘মোশাররফ সাব কোথায়?’
‘আমি জানি না।’
রেগে বললেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি জানো।’
একইভাবে আমার মাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সঙ্গে ছিলেন ছোট খালু এমএম জামাল উদ্দিনের স্ত্রী। তাকেও আর্মিরা জেরা করতে থাকে।
এরপর বলা হলো একটা জায়গার নাম বলতে। যেখানে বাবা লুকিয়ে থাকতে পারেন। ভাবলাম বলে দেখি ওরা কি করে। যশোর পিকনিক কর্নারের পাশে ঘোরাগাছায় অভিনেতা দীন মোহাম্মদের গ্রামের বাড়ি। উনি সম্পর্কে আমাদের মামা হন।
জায়গাটির নাম বলতেই ওরা আমাকেসহ, মা, ছোট খালাম্মা ও তার ছোট ছোট তিনটা বাচ্চাকে মাসুকুর রহমান তোজো ভাইয়ের গাড়িতে উঠাল। ভাই গাড়ি চালান। ওরা সামনে ও পেছনে ওদের জিপে থাকে।ঘোরাগাছায় এসে বাড়িতে ঢুকেই এলোপাতারি গুলি করতে থাকে।
চিৎকার দিয়ে বলে, ‘মোশাররফ সাব, ইধার আও’। কাউকেই পেল না ওরা। তখন আমাদের নিয়ে গেল যশোর ক্যান্টনমেন্টে। তোজো ভাই এক জায়গায় আর আমাদেরকে আরেক জায়গায় রাখে। একের পর এক চলে জিজ্ঞাসাবাদ। একেকজন একেকরকম অস্ত্র নিয়ে আসে। বেয়নেট আর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। বড় চেইন ঘোরাতে ঘোরাতে মারতে আসে। নানাভাবে ভয়ও দেখায়।
একদিন আর্মিরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে চায়। মা শক্ত করে কোমর জড়িয়ে বসে থাকে। কিছুতেই মেয়েকে ছাড়বেন না। কিন্তু আটকেও রাখতে পারে না। ওরা একটা হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে নেয়।
বলে, ‘তোমরা পাকিস্তান ভাঙতে চাও। তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।’ ওরা আমাকে মিছিল করার একটা ফটো দেখায়। তখন অকপটেই স্বীকার করি, ‘হ্যাঁ, আমি মিছিল করেছি, আমি ছাত্রলীগ করি।’
আমাকে এনে দুটো ঘরের সামনে দাঁড় করানো হয়। একটা ঘরে কয়েকটা ছেলেকে হাত-পা ভেঙে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে। রক্তাক্ত শরীর মেঝেতে পড়ে আছে। আরেকটা রুমে ব্যারাক আর্মিদের থাকার বেড। বেডের পাশে বেঁধে রাখা হয়েছে ধরে আনা কয়েকজন নারীকে।
তখন আমাকে ওরা বলে, ‘তোমার বাবা কোথায় আছে, কী তোমাদের পরিকল্পনা?’ সত্যটা বলো। নাহলে ওদের মতো হয় তোমাকে হত্যা করব, না হয় ব্যারাক আর্মিদের সাথে তোমাকে থাকতে হবে।’ শুনে আমি বিচলিত হই না। গোপন সংগঠনের প্রশিক্ষণের কারণেই শক্ত থাকার শক্তিটা পেয়েছিলাম।
উত্তর দিই, ‘বাবা কোথায় আছে জানি না।’ এরপরই আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় কর্নেল তোফায়েলের সামনে। তাকেও বলি, ‘আমি ছাত্রলীগ করি। মিছিলও করেছি। কিন্তু আর কিছু জানি না।’ তখন কর্নেল তোফায়েলকে রিকুয়েস্ট করে বলি, ‘আপনি আমাদের যে বাসা থেকে এনেছেন ওই বাসাতেই নজরবন্দী করে রাখেন। তাহলে আমরাও আপনার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকব।’ খানিক চিন্তা করে কর্নেল কথাটা রাখলেন।”
কর্নেল সাথীদের ওই বাসায় সেন্টি বসিয়ে দেন। সকালে একদল আর রাতে আরেকদল আর্মি পাহারায় থাকত। মাসুকুর রহমান তোজোকেও ছেড়ে দেয় দুদিন টর্চারের পর। তাকে চেইন দিয়ে পিটিয়ে, মুখের বিভিন্ন জায়গায় সুই ঢুকিয়ে টর্চার করে আর্মিরা।
হঠাৎ একদিন দেখি বাড়ির সামনে পাহারা নেই। থানার সামনেও নেই কোনো আর্মি। এ সুযোগে তারা গ্রামের দিকে সরে পড়ার পরিকল্পনা করে।
সাথীর ভাষায়, “ওইসময় পাকিস্তানি আর্মিরা ঘোষণা দেয়, জীবিত বা মৃত মোশাররফ হোসেনকে ধরিয়ে দিলে মোটা অংকের টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। লোকের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে এ খবর। ফলে গ্রামের মানুষ আমাদের আশ্রয় দিতে ভয় পাচ্ছিল। এক গ্রাম পাল্টে আমরা আরেক গ্রামে আশ্রয় নিই।
তোজো ভাই একদিন গাড়ি নিয়ে এসে বলেন, ‘শহরে তেমন আর্মি নেই। এ সুযোগে বর্ডার পার হতে হবে।’ তখন মা, আমার ছোট দুই ভাই-বোন, খালাম্মা আর তার তিনটা বাচ্চাসহ যশোরের চাচড়া মোড় হয়ে বেনাপোল বর্ডার ক্রস করে চলে যাই বনগাঁও। অতঃপর হ্যালেঞ্চা শরণার্থী ক্যাম্পে কাজ শুরু করি।”
কাজ কী ছিল?
তিনি বলেন, “মানুষকে দেখাশোনা, খাবার পৌঁছানো, সহযোগিতা করা এবং বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিলি করাই ছিল কাজ। বনগাঁও করিডোর অফিস ছিল জওপুরে। ওই অফিসের মাধ্যমেই কাজগুলো করতাম। ক্যাম্পটা দেখাশোনা করতেন এসএম জামান উদ্দিন।
ওই ক্যাম্পে তোফায়েল আহমেদ, নুরে আলম জিকু এরা আসতেন, যেতেন। আসতেন বিএলএফ এর কর্মীরাও। বাবা ছিলেন গোবরা শরণার্থী ক্যাম্পের দায়িত্বে। কিন্তু আমি ওখানে না গিয়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে এখানেই কাজ করতে থাকি। নারী হিসেবে এটাই ছিল আমার যুদ্ধ।”
শরণার্থী শিবিরের অবস্থা কেমন দেখেছেন?
রওশন জাহান সাথীর ভাষায়, “খুবই করুণ অবস্থা ছিল। মানুষ আর শেয়াল-কুকুর একসঙ্গে থেকেছে। অন্তসত্ত্বা নারীরা সন্তান জন্ম দিতে গিয়েও মারা গেছে অনেক। তখন ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বর হতো বেশি। বহু মানুষ মারা গেছে এসব রোগে। কলেরার সময় ওষুধের সংকট ছিল বেশি। ভারতের স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেমেয়েরা তখন ওষুধ সংগ্রহ করে দিত। শরণার্থী ক্যাম্পে শিশু ও বৃদ্ধরা মারা গেছে সবচেয়ে বেশি।”
স্বাধীনতা লাভের পর রওশন জাহান সাথী এমএ-তে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা বিভাগে। ১৯৭২ সালের মার্চে বটতলায় ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যায়। আগে থেকেই তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের বিপ্লবী পরিষদের লাইনে চলা লোক। ফলে তাদের সঙ্গেই জাসদ ছাত্রলীগে চলে যান। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন, পরে জাসদ গণবাহিনীরও সদস্য হন। ১৯৭৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা সাথী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ভিপি নির্বাচিত হন।
১৯৭৭ সালের ১৪ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মুক্তিযোদ্ধা রওশন জাহান সাথী। ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের কালিদাসপুর স্কুলমাঠে সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় বক্তৃতাকালে কাজী আরেফকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
পরিবার নিয়ে সাথী তখন বড় বিপর্যের মুখে পড়েন। কাজী আরেফ হত্যায় রাষ্ট্রপক্ষ বাদী হয়ে মামলা করে। কিন্তু আসামীরা সাথীকে নানাভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। সেই হুমকি থেকে মুক্তি মেলেনি এখনও। ওইসময় রাজনৈতিক সহকর্মীদেরও অনেককেই পাশে পাননি সাথী। ফলে কোথায় যাবেন, কার আশ্রয়ে থাকবেন— এ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন।
খবর পেয়ে ডেকে পাঠান বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।
বাকি ঘটনা সাথী বললেন এভাবে, “বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন ডাকলেন তখন মনে হলো একটা ভরসার জায়গা অন্তত পাবো। সব কথা শুনলেন তিনি। অতঃপর সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বললেন, ‘মহিলা শ্রমিকলীগ গড়ব। তুমি দায়িত্ব নিলে খুশি হবো।’
মহিলা শ্রমিকলীগে যোগ দিই তখনই। পরে সম্মেলনের মাধ্যমে আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি করা হয়। এভাবেই নতুনভাবে সংগঠনে কাজ শুরু করি। সতের বছর কাজ করেছি মহিলা শ্রমিকলীগের সঙ্গে। ওইসময় শেখ হাসিনার আশ্রয় না পেলে দুই সন্তানসহ হয়তো আরও দুর্যোগের মুখে পড়ত হতো। পরে তার উদ্যোগেই নবম জাতীয় সংসদে আমাকে মহিলা এমপি করা হয়।”

কথা ওঠে কাজী আরেফ আহমেদকে নিয়ে। সহধর্মিনী ও রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হিসেবে মূল্যায়ন তুলে ধরে সাথী বললেন যেভাবে, “তিনি তো দেশের মানুষ ছিলেন, ফলে কখনও পরিবারের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। তবে সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত শান্ত, ধীর ও দায়িত্ববান ছিলেন। মধ্যবিত্ত মানুষ আমরা। যুদ্ধের সময়ই অঙ্গীকার করেছিলাম খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করব। সেটাই প্র্যাকটিস হয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা ভালোই ছিলাম, আনন্দেই ছিলাম।”
না পওয়ার কোনো আক্ষেপ কি ছিল?
“আক্ষেপ করার সুযোগই ছিল না। কারণ আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে এটাই আমাদের জীবন। ভাবতাম পড়াশোনা করব, জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, জনকল্যাণে কাজ করব। রাজনীতিকেও সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে রাজনৈতিক জীবন ছিল আমাদের কাছে অনেক বড়। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার পরিকল্পনা কখনও আমাদের মনে আসেনি।”
তিনি আরও বলেন, “কাজী আরেফ একজন জাতীয় বীর, জাতীয় নেতা। দেশ যেমন স্বাধীন করেছেন তেমনি জনগণের মুক্তিই ছিল তার আদর্শ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সাজা নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক মুক্তিই তার শেষ কথা ছিল। এ নিয়েই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। কোনো প্রলোভন তাকে কাবু করতে পারেনি। ব্যক্তিগত সম্পদে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। পাঁচটি টাকাও তার ব্যাংকে ছিল না। নেই নিজের কোনো বাড়িও।”
মুক্তিযুদ্ধে বিএলএফ কমান্ডার কাজী আরেফ আহমেদ জীবদ্দশায় মুক্তিযোদ্ধার কোনো কাগুজে সনদ নেননি। কেননা সনদ আর সুবিধার জন্য যুদ্ধ করেননি তিনি। ১৯৬২ সালে দেশ স্বাধীন করার শপথ করেছিলেন, আঙুল কেটে নিজের রক্ত ছুয়ে। মাটি স্পর্শ করেই গিয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু স্বাধীন এ দেশ কি মনে রেখেছে এই বীরকে?

স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও সামান্যতম মূল্যায়ন কি হয়েছে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফের? এমন প্রশ্ন তোলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রওশন জাহান সাথী।
শুধু কাজী আরেফ আহমেদই নয়, বিএলএফ-এর (মুজিববাহিনী) প্রথম কাতারের মুক্তিযোদ্ধা কারোরই জাতীয় বীর হিসেবে কোনো মূল্যায়ন হয়নি। স্বাধীন দেশে যা তাদের প্রাপ্য ছিল। বীরদের মূল্যায়ন বা সম্মানিত না করলে প্রজন্ম কীভাবে বীরত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহিত হবে। তাই এটি আমাদেরও দায়।
তৃণমূলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে আনা ও প্রজন্মকে জানানো, গ্রামপর্যায়ে গণহত্যার জায়গাগুলো চিহিৃত করে সেগুলোকে স্মরণীয় করে রাখা জরুরি বলে মনে করেন এই সূর্যসন্তান। এ ব্যাপারে তরুণদের এগিয়ে আসার দিকেও গুরুত্ব দেন তিনি। ইতিহাসটা জানার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একটা উপলব্ধি, একটা বোধও তৈরি হবে— এমনটাই বিশ্বাস তার।
আগামী প্রজন্মের প্রতি পাহাড়সম আশা বীর মুক্তিযোদ্ধা রওশন জাহান সাথীর। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন শেষ কথাগুলো, “তোমরা দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসো। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রিয় স্বাধীনতা। স্বাধীন এ দেশে তোমরা স্বাধীনতাবিরোধীদের চিনে রেখো। একাত্তরের বীরত্বের ইতিহাসকে হৃদয়ে ধারণ করো। রক্তে পাওয়া এই দেশটাকে তোমাদের হাতেই দিয়ে গেলাম।”
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ২৪ জানুয়ারি ২০২৪
© 2024, https:.