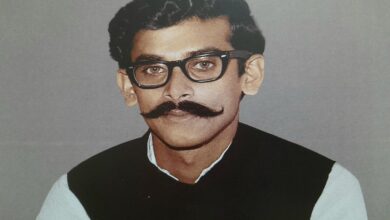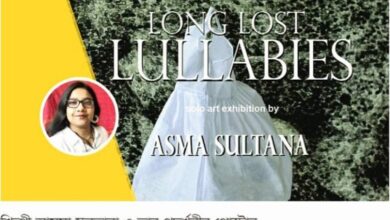১৯৭১: জাঠিভাঙ্গায় গণহত্যা

৭ মার্চ ১৯৭১। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। মুজিবের নির্দেশ ছিল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার। তিনি বলেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়তে। আমাদের কাছে সেটিই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা।
চায়ে চুমুক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হান্নান আবার বলতে শুরু করেন।
ওই সময় আওয়ামীলীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন ফজলুল করিম। তাকে প্রধান করে ঠাকুরগাঁও জেলার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি। কমিটির সদস্য ছিল ৭১ জন।
২৭ মার্চে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রথম শহীদ হয় রিকশাচালক মোহাম্মদ আলী। পরদিন পাক বাহিনী গুলি করে হত্যা করে শিশু নরেশ চৌহানকেও। দ্রুত এ খবর ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। ২৯ মার্চ জেলার ইপিআর ক্যাম্পে বিদ্রোহ করে বাঙালি সৈন্যরা। তারা অস্ত্রাগার লুট করে ব্যাটালিয়ানের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী যেন শহরে ঢুকতে না পারে সেকারণে ওইসময় ২০টি পয়েন্টে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় ঠাকুরগাঁওয়ের সঙ্গে অন্যান্য মহকুমার যোগাযোগ।
শহরটি কতদিন হানাদার মুক্ত ছিল? মুক্তিযোদ্ধা হান্নান বলেন, ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাটি ছিল সৈয়দপুরে। তারা ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। সেখান থেকে তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছিল ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে। তাদের আক্রমণে টিকতে পারে না স্থানীয় মুক্তিকামী মানুষেরা। ফলে আমরা প্রতিরোধ ক্যাম্প তুলে নিয়ে ভারতীয় সীমান্তে অবস্থান নিই।’
১৫ এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বৃষ্টিরমতো গুলি ও শেল নিক্ষেপ করতে করতে গোটা শহরে ঢুকে পড়ে। ঠাকুরগাঁও শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তাদের হাতে। শুরু হয় বাঙালি নিধন। গোটা জেলায় চলে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট আর বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ। এ কাজে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে বিহারীদের একটি অংশ, রাজাকার ও আলবদরের লোকেরা।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান। তাঁর জবানিতে শুনছিলাম ১৯৭১ এ ঠাকুরগাঁও জেলা হানাদার বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার ইতিহাসটি। কথায় কথায় তিনি জানালেন ঠাকুরগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনাটি। সদর উপজেলার জাঠিভাঙ্গা গ্রামে ঘটেছিল সে গণহত্যাটি।
ঠাকুরগাঁও থেকে পঞ্চগড়ের বাসে চেপে বসি আমরা। প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ চলতেই মিলে ভুল্লী বাজার। বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। স্থানীয় একজন জানালেন এটিই ভুল্লী নদী। তাই নদীর নামেই হয়েছে বাজারের নামকরণ।
আমাদের গন্তব্য জাঠিভাঙ্গা। ভুল্লী ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তাটি চলে গেছে সে দিকটাতে। এখানে পথ চলতে ভ্যানই ভরসা। একটি ভ্যান নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে আমরাও এগোই জাঠিভাঙ্গার দিকে।
ইউনিয়নের নাম শুখান পুখরী। কেনো ইউনিয়নটির এমন নামকরণ তা জানা নেই স্থানীয়দের। এ ইউনিয়নকে ঘিরে রেখেছে খরস্রোতা ছোট্ট একটি নদী। সবার কাছে এটি পাথরাজ নদী। নদীর নাম কেন পাথরাজ? এমন প্রশ্নে ভ্যানচালক লোকমান জানালেন নানা তথ্য।
পঞ্চগড় থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এ নদীটি। এক সময় এ নদীতে মিলত অজস্র পাথর। নদীর জলে ভেসে আসত পাথরগুলো। সে পাথর তুলে বিক্রি করতো নদী পাড়ের মানুষেরা। নদীর পাথরে বদলে যেত মানুষের ভাগ্য। তাই নদীপাড়ের মানুষরা নদীটির নাম দিয়েছে পাথরাজ।
জাঠিভাঙ্গা নামক স্থানটি পাথরাজ নদীর তীরেই। শুখান পুখরী ইউনিয়নের এ জায়গাটিতেই ১৯৭১ সালে হত্যা করা হয় কয়েক হাজার নিরীহ-নিরাপরাধ মানুষকে।
যখন জাঠিভাঙ্গায় পৌঁছাই তখন মধ্য বিকেল। নদীর ওপর ছোট্ট একটি ব্রিজ। ব্রিজ বেয়ে রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে জাঠিভাঙ্গা বাজারে। ব্রিজের গোড়াতেই নির্মিত হয়েছে বধ্যভূমির স্মৃতি সৌধটি।
লাল ইটের বেদীর ওপরে কালো টাইলসে বাঁধানো লম্বা প্রাচীর। বিকেলের আলোক ছটা এসে পড়েছে কালো প্রাচীরের ওপরটাতে। দূর থেকে তা জ্বলজ্বল করছে। চারপাশে নদীর তীরঘেষা কলাখেত। সবুজের মাঝে ঝকমকে কালো মিনারটি যেন মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে।
একসময় পাথরাজ নদীর বাঁকে বাঁকে ছিল বাঁশঝাড় আর জংলা। চারপাশ ছিল নিরিবিলি সুনসান। ফলে হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীর দোসররা গণহত্যার জন্য বেছে নেয় এ নদীর তীরটিকেই।
জাঠিভাঙ্গা গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সুধীর চন্দ্র শর্মা। বয়স তার ষাটের মতো। ১৯৭১ সালে ছিলেন যুবক বয়সী। সেদিন দূর থেকে গণহত্যায় স্থুপ করা লাশ দেখে তিনি আৎকে ওঠেন। তখনও কয়েকজন ছিলেন জীবিত। বেয়নেটের আঘাতে নিথর করে দেয়া হয় তাদের দেহ। নিভে যায় তাদের জীবন প্রদীপ। গণহত্যার ঘটনাটি শুনি সুধীরের মুখেই।
১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। শুক্রবার। দুপুরের পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী পাশের জগন্নাথপুর, নাড়–পাড়া, পলাশবাড়ীসহ দক্ষিণের গ্রামগুলো থেকে ধরে আনে মুক্তিকামী নিরীহ লোকদের। অন্যদিকে ভারতে যাওয়ার পথে ধরে আনা হয় কয়েক হাজার হিন্দু বাঙালীকে। পরে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হবে ভারতে—এমন আশ্বাসে জড়ো করা হয় সবাইকে। এ কাজে তাদের সহযোগিতা করে স্থানীয় রাজাকার ও আল বদরের লোকেরা। জাঠিভাঙ্গায় নদীর ধারে প্রথমে লুটপাট করে কেড়ে নেয়া হয় সকলের টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার। অতঃপর ব্রাশ ফায়ারের গুলিতে সবাইকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হয় পাথরাজ নদীর তীরে। রক্তে লাল হয় পাথরাজের জল। নদীর জলে ভেসে যায় মানবতা।
সুধীর বলেন, ‘প্রায় দুই হাজারের ওপর লোককে হত্যা করা হয়েছিল এখানে। এখনো জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুরে গেলে দেখা মিলে শত শত বিধবার। স্বামীকে হারিয়ে সেদিনের বীভৎস স্মৃতি নিয়ে আজো বেঁচে আছেন তারা। স্বাধীনের পর অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে তাদের জীবন। তবুও, রাষ্ট্রীয়ভাবে মেলেনি শহীদ পরিবারের সম্মান ও স্বীকৃতিটুকু।’
জাঠিভাঙ্গা বাজারে মেলে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিমের দেখা। স্মৃতিসৌধের জন্য জায়গাটি দিয়েছেন তারই বড় ভাই আব্দুর রশিদ। বধ্যভ‚মিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হলেও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই। তিনি দাবী জানান, জাঠিভাঙ্গা গণহত্যায় শহীদ পরিবারগুলোকে সরকারি স্বীকৃতি ও পুনর্বাসনের।
জাঠিভাঙ্গায় শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধের প্রধান গেইট ও সীমানা প্রাচীরের কোনো অস্তিত্ব চোখে পড়ল না। স্মৃতিসৌধের পেছন দিকটা অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। বোঝার অপেক্ষা রাখে না বহুদিন কারো পায়ের ছাপ পড়েনি এখানটাতে। স্মৃতিসৌধের কোথাও গণহত্যার ইতিহাসটি টাঙানো নেই। ফলে কেন এই স্মৃতিসৌধটি—তা জানার উপায় নেই আগতদের। স্থানীয় কয়েকজন যুবককে প্রশ্ন করতেই তারা শুধু বললেন, একাত্তরে কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছে এখানে। তারা সঠিকভাবে জানেও না এখানকার গণহত্যার ইতিহাসটি।
এ প্রসঙ্গে উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সাবেক কমান্ডার বলেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ের সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল জাঠিভাঙ্গায়। তাই পরবর্তী প্রজম্মের কাছে এ ইতিহাসটি তুলে ধরা প্রয়োজন ।’
স্মৃতিসৌধ শুধু ইট সুরকির কোনো স্থাপনা নয়। এটি শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মানের নিদর্শনও। অথচ বছরের বিশেষ দিনেও ফুলেল শ্রদ্ধা পড়ে না জাঠিভাঙ্গা স্মৃতিসৌধে। নেই সংস্কার আর নিয়মিত পরিচর্চার ব্যবস্থা। নেই কোনো স্থানীয় উদ্যোগও। যা দেখে আজ শহীদ পরিবারগুলো শুধুই নিরবে চোখের জল ফেলে।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপ্রকাশে, প্রকাশকাল: ৩১ মার্চ ২০২৩
© 2023, https:.