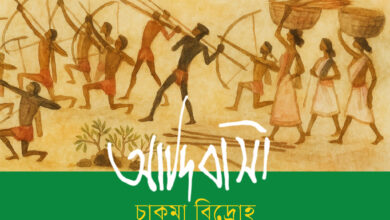বহবলদিঘীর ভুনজাররা

ইউনিয়নের নামটি অন্যরকম। বহবলদিঘী। একসময় ‘বহবল’ নামে একটি দিঘী ছিল। পরে গোটা ইউনিয়নের নামকরণ হয় ওই দিঘীর নামেই। দিনাজপুরের বিরল উপজেলার এ ইউনিয়নেই বসবাস নানা জাতির আদিবাসীদের। এমন তথ্য জেনেই রওনা হই আদিবাসীদের জীবনযাত্রা দেখার ইচ্ছে নিয়ে।
পাকা রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ। চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধুই ধান ক্ষেত। সবুজ-সোনালী রঙের থোকা থোকা ধান ঝুলছে ফসলের মাঠে। দেখতে বেশ লাগছে। ধান কাটার সময় আগত প্রায়। গ্রামের কৃষকদের মুখে তাই আনন্দের হাঁসি খেলছে।
একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন বৃদ্ধার দেখা মিলল। বেশ আয়েশ করে চা খাচ্ছেন তারা। চলছে নানা গল্প-গুজবও। এবার ধান কেমন হবে, দাম কত হবে, লাভ হবে কিনা—এসব নিয়ে চলছে তর্কের ফুলঝুড়ি। কারো কারো মুখে আদিবাসী পাইট বা কাদর খোঁজার কথাও হচ্ছিল। তাদের পাবেন কিনা— এ নিয়ে আফসোসও করছেন কেউ কেউ। কেন? কারণ খুব অল্প সময়ে মাঠের ফসল ঘরে তুলতে আদিবাসী পাইটদের (শ্রমিক) কোন বিকল্প নেই। আর এ কারণেই ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়দের আনাগোনা শুরু হয় আদিবাসী গ্রামগুলোতে।
ভাদ্র, আশ্বিণ ও কার্তিক— এ তিন মাস অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকা আদিবাসীদের কেউ খোঁজ না করলেও অগ্রাহয়ণে এদের কদর যায় বেড়ে। এ সময়ে অনেকেই আবার অধিক মজুরীর প্রলোভন দেখায় তাদের। গোটা বহবলদিঘীতেই নানা আদিবাসী জাতির বাস। গ্রামের পাশেই ঘন সবুজ শালবন। একসময় এ শালবনকে ঘিরেই চলতো আদি মানুষদের জীবন, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রবাহ।
নানা চিন্তার ঘোর কাটার আগেই পৌঁছে যাই বহবলদিঘী বাজারে। রাস্তার এক পাশে বড় কালিমন্দির। কালি পূজাতে এখানে শত শত পশু বলি দেয়া হয়। অন্য পাশে রাস্তা ঘেষা বেশ কিছু মাটির দেয়াল। ভেতরে বিশ পচিঁশটি বাড়ি। বাহিরের দেয়াল দেখে ভেতরের বাড়িরগুলোর অবস্থা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। একটি বাড়ির দরজা ঢেলে ভেতরে ঢুকতেই চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। খড়ে ছাওয়া মাটির ছোট ছোট ঘরগুলো বিধস্ত হয়েও কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে।
এখানেই জীবন চলছে কয়েকটি আদিবাসী পরিবারের। পাশে থাকা দেবী কালির সুনজর পড়েনি তাদের ওপর। আলাপচারিতায় মধ্যবয়সী উষার কাছে জানতে চাই তাদের জাতির নামটি। কিছুটা শঙ্কা আর চিন্তিত মুখে সে বলল, ‘বাবু, হামনি ভুনজার জাতি’।
কবে থেকে এই আদি মানুষগুলো এখানে? প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভুনজার গোত্রের মহত বাতাসু ভুনজার। তার ভাষায় তিনি বলেন, ‘এ ডাঙ্গা পার খুবে জঙ্গল ছেলে, কাটি কুটি বসত কার লেসে’। মহতের সাথে নানা বিষয়ে গল্প জমে উঠতেই বাড়ীর এক কোনায় ভাঙ্গাচোরা দুটি পালকি নজরে এলো। টিন আর কাঠের তৈরি পালকি দুটি পুরনো হলেও যথেষ্ট যত্নসহকারেই রাখা।
এক সময় বাঙালি বিয়েতেই পালকির ব্যবহার ছিল। সে সময়ে পালকির প্রয়োজনে সকলকেই আসতে হতো ভুনজারদের এই আদিবাসী গ্রামটিতে। এখন সময়ের হাওয়ায় বদলে গেছে বিয়ের আদি রীতিগুলো। ফলে বিয়ের আচার থেকে পালকির প্রচলনও উঠে গেছে। পালকি এখন রূপকথার হিমঘরে কোন রকমে টিকিয়ে রাখছে নিজেকে। তবে মহত জানালেন শীত মৌসুমে এখনো কোন বিত্তশালীর বিয়েতে ডাক পড়ে ভুনজার গ্রামের পালকি সর্দার গমেশ ভুনজারের। পালকি টানার আনন্দে গমেশ তখন নিজ ভাষায় ডাকতে থাকে অন্যদের— ‘পালকি বোহেল লাগতে’।
গ্রামের একটি বাড়ির প্রায় পুরোটাই ভাঙ্গা। তারপরও উঠানে অন্যরকম শক্তি নিয়ে বেঁচে আছে ভুনজারদের গৃহ দেবতা ‘তুলসী’। সেই তুলসীর সামনে বিনীত ভঙ্গিতে ধুপ জ্বালিয়ে, উলু ধ্বনি দিয়ে ভক্তি দিচ্ছে ছোট্ট একটি মেয়ে। নাম বলল, রিতা ভুনজার। কোন পূজায় বেশী আনন্দ জানতে চাইলে এক বাক্যে রিতার উত্তর ‘বিশহরি’।
দেবী দুর্গা ও কালির খুব বেশী প্রভাব এ আদিবাসীদের মধ্যে নেই। এদের প্রাণের দেবী মনসা। দেবী মনসাকে ভুনজাররা ডাকে ‘বিশহরি’ নামে। এ আদিবাসীদের বিশ্বাস বিশহরিই তাদের জিন্দা দেবতা। বিশহরির শক্তিতেই তারা সাপে কাটা ব্যক্তিকে মন্ত্র দিয়ে ভালো করেন।
এ অঞ্চলে কাউকে সাপে কাটলে সকলেরই শেষ ভরসা আদিবাসী ভুনজাররা। কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই এরা সাপে কাটা রোগীকে মন্ত্র দিয়ে সুস্থ করে তোলে। কি সে মন্ত্র? পাশ থেকে ভাসাই ভুনজার হরহর করে বলতে থাকেন বিষ নামানোর মন্ত্রটি— ‘সাপা বলে শোন সাপেনি, গোগনেরই কথা, পঞ্চম তালের বিষ, জন্ম হলো কথা’।
ভাসাই বললেন, ভাদ্র মাসের চাঁদের পুর্ণিমার দিন তারা পালন করেন বিশহরি পূজা। গোটা গ্রামে তিনদিন ধরে চলে এটি। প্রথমদিন গোত্রের সবাইকে উপোস থাকতে হয়। বিশহরি দেবীকে খুশি করাই উপোসের উদ্দেশ্য। উপোস অবস্থায় খাওয়া যায় শুধুই ফল আর দুধ। ওইদিন সকলেই একত্রিত হয়ে পূজা দিয়ে বিশহরিকে জানায় মনের নানা ইচ্ছের কথা।
দ্বিতীয় দিনে দেবীর সন্তুষ্টিতে হাঁস বলি দেওয়া হয়। সারা বছর ভুনজাররা যে কয়টি সাপে কাটা রোগীকে ভালো করেন সেকয়জনকে এই পূজায় বিশহরির সন্তুষ্টির জন্য এক বা একাধিক হাঁস দান করতে হয়। অতঃপর নিজেদের ও দানের হাঁসগুলোকে একে একে বিশহরির উদ্দেশ্যে বলি দেয় তারা। এ সময় তাদের কণ্ঠে ওঠে বিশহরির গান—‘মন দুঃখে কান্দে, পদ্মা নিধুয়া বলে’। বলি দেয়া হাঁসগুলো দিয়ে মহতের বাড়ীতে সকলের জন্য রান্না হয় খিচুরি। সারারাত চলে ভুনজারদের ‘ঝুমটা নাচ’ এর আসর। চলে প্রিয় পানীয় হাড়িয়া আর চুয়ানী খাওয়াও।
তৃতীয় দিন পরম ভক্তির সঙ্গে নিকটস্থ নদী বা খাল বা পুকুরে বিশহরিকে বির্সজন দেয় ভুনজাররা। বিশহরি ছাড়াও এ আদিবাসীদের মধ্যে ঢোলপূজা পালনের আধিক্য দেখা যায়। ফাগুণ মাসের পূর্ণিমার চাঁদে তারা এ পূজা পালন করে থাকে।
পূজার গল্পে যখন বিভোর ঠিক তখনই একটি ঘর থেকে এক নবজাতকের কান্নার শব্দ পাই। মাত্র দুদিন আগেই জনতা ভুনজারের কোলে জন্ম নিয়েছে নবজাতকটি। গোত্রের মহত জানালেন নবজাতকদের নিয়ে তাদের নানা আচারগুলো। যে দিন বাচ্চার নাভি পড়বে সেদিন ভুনজাররা তাদের পূর্বপুরুষদের বিধান মতে বাড়ীতে ডেকে আনে নাপিত ঠাকুরকে। নাপিত গোটা গ্রামের প্রত্যেকের চুল ও দাড়ি কামিয়ে দেয়। পাশাপাশি নারীদের কানি আঙ্গুলের নখ ব্লেড দিয়ে সামান্য ঘষে দেয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এতে সকলেরই শুদ্ধি ঘটে। অতঃপর মিষ্টি মুখ করানো হয় সবাইকে।
মহত জানান এ আদিবাসীরা অন্নপ্রশান অনুষ্ঠানের পূর্বে তাদের নবজাতকে কোন নামেই ডাকেন না। তাদের ভাষায়, ‘ নাম রাখেল রাখতে বুতুর টুর’। অন্নপ্রশানের দিন বাড়ীতে ডাকা হয় গোসাই ঠাকুর বা সাধু বাবাকে। সাধু বাবা দুধ, কলা, বাতাসা, চিনি, মধু ও ঘি একত্রিত করে বিশেষ ধরণের খির তৈরি করেন। অতঃপর বাড়ীর তুলসী দেবতার সামনে যোগ পূজা দেন। পূজার পরে নবজাতকের দাদা-দাদী ওই খির তার মুখে দিয়ে সুন্দর নাম রাখে। অতিথিরা একে একে তুলে দেয় তাদের উপহারগুলো। এরপরই সকলকে খিরসহ খাওয়ানো হয় ভাত আর নিরামিষ। মূলত আদিবাসী সংস্কৃতি থেকেই এমন অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতিতেও স্থান করে নিয়েছে বলে মনে করেন অনেকেই।
কথা হয় গ্রামের সুশিল ভুনজারের সঙ্গে। তার সময় যেন কাটছেই না। অগ্রহায়ণের অপেক্ষায় আছেন। এ অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো ভুনজারদেরও তিন মাসের কষ্টের অবসান ঘটে অগ্রহায়ণে। এটি ফসল কাটার মাস। ফসল কাটার প্রথম দিনে ভুনজাররা পালন করে বেশ কিছু আচার। এ উৎসবটিকে তারা বলে ‘লবান’। মূলত আদিবাসীদের এই লবান উৎসব থেকেই নবান্ন উৎসবের প্রচলন ঘটেছে।
ফসল কাটার প্রথম দিনে এ আদিবাসীরা প্রত্যেক বাড়িতে আলাদা আলাদা ভাবে পালন করে ‘লবান’। বাড়ীর যে কোন একজনকে উপোস অবস্থায় যেতে হয় ধান কাটতে। এর মধ্যেই মহিলারা মাটি দিয়ে বাড়ীর উঠান লেপে পরিস্কার করে রাখে। মাঠ থেকে কিছু ধান কেটে এনে রাখা হয় বাড়ীর পরিস্কার উঠানে। সেখানে সিন্দুর ও ধুপ জ্বালিয়ে পূজা দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে মুরগী বলি দেয় ভুনজাররা। অতঃপর মাঠ থেকে আনা ধান মারিয়ে নতুন চাল তুলে খিচুরি রান্না করে এ আদিবাসীরা। এ খিচুরি খেয়েই উপোসকারী উপোস ভাঙ্গে। এর পরেই আনন্দের সঙ্গে চলে হাড়িয়া আর চুয়ানী খাওয়া। এটিই ‘লবান’ উৎসব। তাই অগ্রায়হণের আগেই ভুনজাররা বলতে থাকে, ‘ইন্ম লবান নালা লাগগো’।
ভুনজারদের গ্রামে দু’এক পরিবার ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। নিজের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হওয়ার কষ্টবোধ ভাসাই ভুনজারকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। অভাব দূর করতে ধর্মান্তরিত হওয়া যায়, কিন্তু মন থেকে কি ধর্ম বিশ্বাসকে সত্যিকার অর্থে বদলানো যায় বাবু? ভাসাই ভুনজারের কথায় বাকিরাও নিরব থাকেন।
সবাই কেন ধর্মান্তরিত হলেন না? এমন প্রশ্ন শুনে মলিন মুখে উঠে যান কয়েকজন। প্রশ্ন শুনে উঠানের এককোণ থেকে জনতা ভুনজার গর্জে ওঠেন, উচ্চ কন্ঠে বলেন, ‘যেটাই জন্ম হইয়া আইছি সেটাই মৃত্যু হমু’।
জনতা ভুনজারের প্রতিবাদের ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে। অভাব-অনটন নিত্য সঙ্গী আদিবাসী পরিবারগুলোতে। তবুও তা মেনে নিয়েই আদি বিশ্বাসগুলো মনের ভেতর আগলে রেখেছেন এ গ্রামের ভুনজাররা। অন্যরকম এক প্রাণশক্তি নিয়েই টিকে আছে ভুনজার জাতির আদিবাসীরা।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপ্রকাশে, প্রকাশকাল: ২০ জুলাই ২০২৩
© 2023, https:.