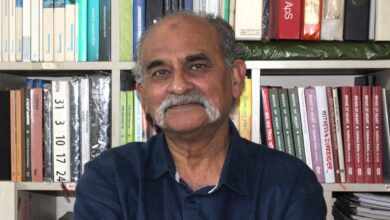জীবনের মায়া একাত্তরে ছিল না

“আমগো বাড়ি ছিল পদ্মার পাড়ে। চর এলাকা। দিনভর নদীর বুকে সাঁতার কাটতাম। মাঝেমধ্যে মাছ ধরতাম বালিজাল দিয়া। আনন্দ ছিল অন্যরকম। কলার ভেলা বানাতাম বন্ধু ইউসুফ ও হাসনকে নিয়া। ভাদ্র মাসের দিনগুলোতে আমরা নৌকা নিয়া ঘুরতাম। ইলিশ ভাজার গন্ধে তৃপ্ত হতাম। এখনও মনে হলে জিভে জল এসে যায়।”
“আমার দাদা বশির মোল্লা ছিলেন নামকরা লাঠিয়াল। কিন্তু তিনি কোনো অন্যায় কাজে যেতেন না। বরং অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করতেন। দশ গ্রামের মানুষ তাকে মান্য করত। বেয়াদবি দেখলেই তিনি আমগো কান ধরে উঠবোস করাতেন। মাথায় কাপড় ছাড়া কোনো নারী তার সামনে দিয়া যেতে পারত না। তা ঘটলে ডেকে আনা হতো তার স্বামীকে। কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। নিরক্ষর হয়েও বলতেন, শিক্ষা হলো আলোর মতো।”
“পঁয়ষট্টিতে যুদ্ধ হয় ভারত-পাকিস্তান। ওই যুদ্ধের বাজনা ও চরমপত্র আগ্রহ নিয়ে শুনতাম রেডিওতে। দেশ তখন অশান্ত। সবার মুখে শেখ মুজিবের নাম। তখনো তাকে দেখিনি। বড়রা বলতেন তিনিই আমাদের জন্য লড়াই করছেন। রেডিওর নানা খবরাখবর আর মুরুব্বিদের আলোচনা থেকেই জেনে যেতাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যগুলো।

৭ মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে। সে ভাষণ আমরা শুনি রেডিওতে। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি…।’ রক্ত তখন টলমল করছিল।
২৫ মার্চ ১৯৭১। সারা দেশে পাকিস্তানি আর্মি নামে গণহত্যায়। আমগো দুগলিয়া বাজারে ক্যাম্প বসায় রাজাকাররা। জব্বার ছিল ওই ক্যাম্পের সার্বিক দায়িত্বে। সামাদ কমান্ডে। পাবনায় রাজাকারগো বড় নেতা মতিউর রহমান নিজামী। গ্রামের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। শুধু মজিদ চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু পক্ষের লোক।
ওই সময় রাজাকাররা যাদের ধরে নিয়ে যেত তারা আর ফিরে আসত না। একবার বাবর আলী নামে এক আত্মীয়কে তুলে নেয় ওরা। পরে তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। রাজাকাররা বেশি অত্যাচার চালাত বাঙালি হিন্দু এলাকায়। লুটে নিত তাদের সর্বেস্ব। যুবতী দেখলেই ধরে নিয়ে যেত আর্মি ক্যাম্পে। চোখের সামনে এসব দেখে ঠিক থাকতে পারতাম না। এই অন্যায় তো সহ্য করা যায় না। একদিন মনটা খুব অস্থির হয়। ওইদিনই সিদ্ধান্ত নিই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার।”
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কারণ এভাবেই বলছিলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো. কেয়ামউদ্দিন মোল্লা। ইসারত মোল্লা ও খোদেজা খাতুনের সাত সন্তানের মধ্যে কেয়াম সবার বড়। তার বাড়ি পাবনা সদর উপজেলার দীঘি গোয়েল গ্রামে। তাদের বাড়ি ছিল চর এলাকায়। আশপাশে ছিল না কোনো স্কুল। বংশের ভেতরও কেউ লেখাপড়া করেনি। ফলে অন্যদের মতো কেয়ামউদ্দিনেরও লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি।
মুক্তিযুদ্ধের অল্প কিছুদিন আগেই বিয়ে করেন কেয়ামউদ্দিন। নববধুকে ফেলে, পরিবারকে না জানিয়ে তিনি ঘর ছাড়েন দেশের টানে। যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে।
কীভাবে? সে ইতিহাস শুনি তার জবানিতে-
“মা ও বউয়ের মায়ার টান ছিল বেশি। তাই না জানিয়েই যুদ্ধে যাই। একদিন খুব ভোরে রওনা দিয়ে চলে আসি কুষ্টিয়ায়। সঙ্গে ছিল ইয়াকুব আলী ও সিদ্দিকসহ গ্রামের চারজন। হেঁটে রাতের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাই বর্ডারে। পরদিন সকালে আসি ভারতের কেচুয়াডাঙ্গা বাজারে। ওখানেই মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাই। প্রথমে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় দোলঙ্গি হয়ে মালদাহর গোরবাগানে। সেখানে তেরো দিন চলে লেফট-রাইট। অতঃপর ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির পানিঘাটায়। আটাশ দিনের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের। এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নং ছিল ৭৭৪৯।”
ট্রেনিং শেষে কেয়ামউদ্দিনদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তরঙ্গপুরের কালিয়াগঞ্জে। অস্ত্র দেওয়া হয় ওখান থেকেই। ওই ক্যাম্পের কথা উঠতেই তিনি বলেন, “চার হাজার লোক খেত এক নোঙ্গরে। দুপুর দুইটায় দাঁড়ালে খানা মিলত চারটায়।”

অস্ত্র নিয়ে সাত নম্বর সেক্টরের দোলঙ্গি ক্যাম্প হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন কেয়ামউদ্দিনরা। তারা ছিলেন গেরিলা। আত্মগোপন করে থাকতেন দেশের ভেতরেই। তাদের তেত্রিশজনের দলটির কমান্ড করতেন রশিদ সরদার।
কোথায় কোথায় অপারেশন করেন?
মুক্তিযোদ্ধা কেয়াম উত্তরে বলেন, “দিনের বেলায় আমরা ইনফরমেশন নিতাম। আর রাতে পরিকল্পনামতো চলত অপারেশন। অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিতাম ব্রিজগুলো। অবকাঠামো ও পাকিস্তানি সেনাদের আসা-যাওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়াই ছিল গেরিলাদের প্রধান কাজ। জীবনের মায়া তখন ছিল না। আমরা অপারেশন করি সাত নম্বর সেক্টরের লালপুর, ভেড়ামারা, সুজানগর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকায়।”
মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষদের সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা বলেন, “মানুষের বাড়িতে আমরা লুকিয়ে থাকতাম। নিজে না খেয়ে অনেকেই আমাদের খাওয়াতেন। গরীব ঘর হলে আমরা খরচটা দিতাম। কিন্তু সেটা নিতে চাইত না কেউ।”
ঈশ্বরদীর বাবুচরা গ্রাম থেকে কেয়ামরা চলে আসেন পাবনায়। অন্যান্য জায়গা থেকে আসে আরো কয়েকটি দল। রাতে সবাই মিলে পরিকল্পনা করেন পাবনার ‘মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল’ দখলে নেওয়ার। ওখানে ছিল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটি। চার গ্রুপে তারা দুই শ জনের মতো। কমান্ডে ছিলেন পাবনার রফিকুল ইসলাম বকুল। কয়েকটা উপদলে ভাগ হয়ে আক্রমণ করেন তারা। তারপর কিয়ামরা ফিরে আসেন বাবুচরাতে।
কী ঘটেছিল রক্তাক্ত ওই দিনে? প্রশ্ন শুনে কেয়ামউদ্দিন আনমনা হন। খানিক নীরবতা। তারপর বলেন ওইদিনের আদ্যোপান্ত।
তার ভাষায়- “সুজানগর থানা অপারেশনের পরিকল্পনা করি আমরা। ওখানে ছিল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটি। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। সন্ধ্যারাত। কয়েকটা দলে আমরা তেত্রিশজন গেরিলা। প্রথম ফায়ার করবে পশ্চিম ও দক্ষিণের গ্রুপ। তেমনটাই ছিল পরিকল্পনা। আমি পশ্চিমের গ্রুপে। পজিশনে যেতেই ওরা দেখে ফেলে। শুরু হয় গোলাগুলি। পাকিস্তানি সেনাদের কাছে ছিল অত্যাধুনিক সব অস্ত্র। আমরা টিকতে পারছিলাম না। ক্রলিং করে সামনে এগোই। পাশেই এলএমজি চালাচ্ছেন সেলিম। হঠাৎ ‘চু’ করে একটা শব্দ হয়। তাকিয়ে দেখি গুলি লেগেছে ওর মাথায়। শরীরটায় কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়েই ও নিথর হয়ে যায়। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখলাম। ওর কাছেও যেতে পারিনি। মনের ভেতর তখন মৃত্যুভয়। কিছুক্ষণ পর পেছনে হটতে নির্দেশ দেন কমান্ডার রশিদ সরদার।”
“গুলি চালিয়ে আমি পেছনে যাওযার চেষ্টা করি। ওই সময়ই দুটি গুলি এসে লাগে শরীরে। একটি আমার সোয়েটারের ভেতর আটকে যায়। অন্যটি ডান হাতে বিদ্ধ হয়। হাত থেকে তিরতির করে রক্ত বেরোচ্ছিল। হাতে কোনো বল নেই। তখন হাত আর নাড়াতে পারি না।”

“সহযোদ্ধারা এসে আমায় তুলে নেয়। গরুর গাড়িতে করে পাঠানো হয় বাবুচরায়। তখনো জ্ঞান আছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। পানি পিপাসায় ছটফট করছি। কিন্তু কেউ তো পানি দেয় না। পানি খেলেই মৃত্যু অবধারিত। তাই সমরে আহত কাউকেই পানি দেওয়া হতো না।
“বাবুচরায় আমাদের সঙ্গে এক ডাক্তার ছিলেন। তিনিই হাত থেকে গুলিটি বের করে সেলাই করে দেন। পরবর্তীকালে হাতের চিকিৎসা হয় কলকাতায়। গুলিতে আমার ডান হাতের হাড় ফেটে গিয়ে কয়েকটি রগ ছিঁড়ে যায়। হাতটি কাটা থেকে রক্ষা পেলেও সারাজীবনের জন্য তা অকেজো হয়ে যায়।”
মুক্তিযুদ্ধকে সাধারণ মানুষের যুদ্ধ বলেন মনে করেন মুক্তিযোদ্ধা কেয়ামউদ্দিন।
তিনি বলেন, “শতকরা ৮৮ জনই ছিল কৃষক ও সাধারণ ছাত্র। বড়লোকের ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে খুব কম। অনেকেই জীবন বাঁচাতে চলে গিয়েছিল ভারতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় প্রধান সংগঠক ছিলেন নাসিম সাহেব। মাঠে ছিলেন ইকবাল, রফিক, কাজী আরেফ, বকুল প্রমুখ।”
মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রসঙ্গে কেয়ামউদ্দিন অকপটে তুলে ধরেন নিজের মতামত।
তার ভাষায়- “স্বাধীনতা লাভের পরপরই ছিল তালিকা তৈরির উপযুক্ত সময়। কতজন ভারতে ট্রেনিং নিয়েছিল, কতজন মুজিব বাহিনী ও কাদের বাহিনীতে ছিল, এসব তথ্য তখন এক করলেই মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হয়ে যেত। তার আগেই রাজাকারদের তালিকা করা বেশি দরকার ছিল। কিন্তু সেটিও হয়নি। এখন তো মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাটাই রাজনৈতিক প্যাঁচে পড়েছে। আমার মতে, দুই লাখ পঁচিশ হাজারের বেশি মুক্তিযোদ্ধা নেই। এর মধ্যে পঁচিশ হাজার আর্মি। বাকিরা ছাত্র-জনতা। সুবিধা লাভের আশায় তালিকা শুধু বাড়ছে। তবে যাচাই করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা ফাইনাল করা উচিত। কয়েকদিন পরপর যাচাই-বাছাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সত্যি অস্বস্তিকর।”
‘স্বাধীনতার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা বির্তকিত হয়েছেন’, মনে করেন কেয়ামউদ্দিন।
তিনি বলেন, “স্বাধীনের পর আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত হই। ডিফেন্সের মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, তারাই দেশটা স্বাধীন করেছেন, মুজিববাহিনীর লোকেরা বলেন, তারাই ছিলেন প্রধান ভূমিকায় আর আমরা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা বলি, আমরাই তো যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। এটা আমাদের জন্য খারাপ হয়েছে। আমরা তো কোনো দলের নই। আমার শুধুই মুক্তিযোদ্ধা।’
মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, “গ্রাম পর্যায়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে না খেয়ে থাকতে দেখেছি। আমার আয় দিয়ে পরিবার চলত না। বহু কষ্টে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়েছি। কিন্তু এখন সেটা নেই বললেই চলে। শেখ হাসিনা সরকার আমাদের সম্মান দিয়েছে। ভাতা বাড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা মাথা তুলে বাঁচতে পারছি। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে!”
“বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ চলতে থাকে উল্টো পথে। জিয়া কোলে তুলে নেন স্বাধীনতাবিরোধীদের। ইতিহাস হয় কলঙ্কিত। মুক্তিযোদ্ধাদের তখন কোনো দামই ছিল না। পরে রাজাকাররা হয় দেশের মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। মুক্তিযোদ্ধাদের তখন মরে যেতে ইচ্ছে করত। ক্ষমতার লোভ যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াই তার উদাহরণ। ইতিহাসের এ দায় থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না”, বলেন কেয়ামউদ্দিন।
স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভালো লাগার অনুভূতি জানতে চাই আমরা।

উত্তরে এই সূর্যসন্তান বলেন, “দেশের উন্নয়ন দেখলে ভালো লাগে। এদেশের সোনার ছেলেরা যখন বিদেশের মাটিতে খেলায় জেতে বাংলাদেশের পতাকাকে সম্মানিত করে, তখন গর্বে বুক ভরে যায়। আগে তো দেশের কোনো লক্ষ্য ছিল না। ছিল না কোনো স্বপ্ন। সরকারের মাধ্যমে এখন সবাই স্বপ্ন দেখছি। ২০৪১ সালে হবে উন্নত বাংলাদেশ। ভাবলেই ভালো লাগে।”
খারাপ লাগে কখন?
“রাজাকারের ছায়া দেখলেই খারাপ লাগে। যারা দুর্নীতি করছে তাদের দেখলে ঘৃণা আসে। কিছু খারাপ লোক রাতারাতি বড়লোক বনে যাচ্ছে। কীভাবে কেউ জানে না। আমরা চেয়েছিলাম সোনার বাংলা। এখনো সেটা আছে, তবে শুধু মুখে মুখে।”
মুক্তিযোদ্ধা কেয়াম বিশ্বাস করেন, দেশের জন্য ভালো কী হবে তা ঠিকই বুঝে নিতে পারবে পরবর্তী প্রজম্ম।
চোখেমুখে আলো ছড়িয়ে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “তোমরা দেশের গৌরবের ইতিহাসটা জেনে নিও। দেশের স্বার্থে এক হয়ে কাজ করো। দেশটাকে ভালোবেসো। মনে রেখো, অনেক রক্ত আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই দেশ। তোমাদের হাত ধরে দেশটা উন্নত হলেই শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।”
সংক্ষিপ্ত তথ্য
নাম : যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো. কেয়ামউদ্দিন মোল্লা।
ট্রেনিং : ২৮ দিনের ট্রেনিং করেন শিলিগুড়ির পানিঘাটায়। এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নং–৭৭৪৯।
যুদ্ধ করেন : সাত নম্বর সেক্টরের পাবনা, লালপুর, ভেড়ামারা, সুজানগর, ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকায়।
যুদ্ধাহত : ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। সন্ধ্যায়। সুজানগর থানা অপারেশনের সময় ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাতের হাড় ফেটে যায়। ছিঁড়ে যায় অনেকগুলো রক্তনালী। ফলে চিরদিনের জন্য হাতটি কার্যক্ষমতা হারায়।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ২১ ডিসেম্বর ২০১৭
বই সংবাদ:
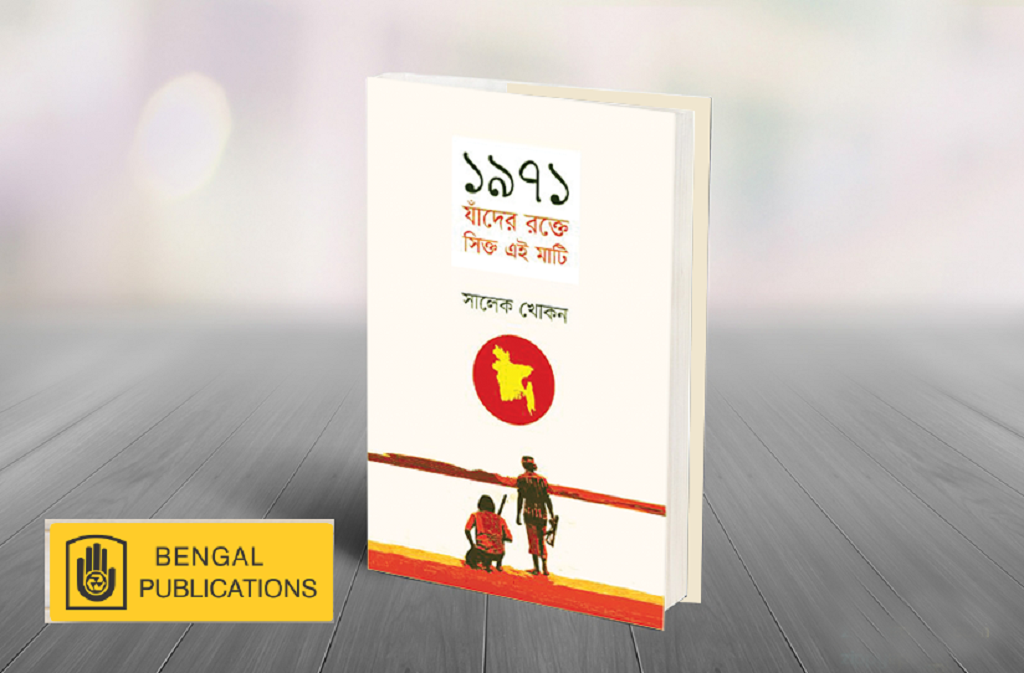
এই লেখাটিসহ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরও দুঃসাহসীক কাহিনি নিয়ে বেঙ্গল পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে ‘১৯৭১: যাঁদের রক্তে সিক্ত এই মাটি’ গ্রন্থটি।
© 2018, https:.